শিল্পকলার অগ্রগতিতে বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে আসছে। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় কলকাতায় প্রথম এই ধরণের সংগঠনের জন্ম হয় ১৮৩০ সালে, যার নাম 'ব্রাশ ক্লাব' (Brush Club)। কয়েকজন ভারতীয় ও ব্রিটিশ উদ্যোক্তাদের মধ্যে মধ্যমনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এর আয়ু ছিল স্বল্পকাল। এরপর কালে কালে এক এক করে অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বল্পায়ু নিয়ে। একমাত্র ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট (Indian Society of Oriental Art) এখনও সক্রিয়। সাম্প্রতিক কালে এই রকম কয়েকটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের একটি হলো প্রিন্সেপস (Prinseps)।
প্রিন্সেপস (Prinseps) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হলো 'ফার্স্ট' (First) অথবা 'ফোরমোস্ট' (Foremost)। মূলত এটি একটি অকশন হাউস (Auction House) হলেও শিল্প সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নে নানারকম যুগোপযোগী কাজ করে চলেছে। যেমন শিল্পবস্তু বিক্রয়, অবলুপ্তপ্রায় শিল্প ইতিহাস পুনরুদ্ধার, আর্ট ও টেকনোলজির সাথে সম্পর্ক স্থাপন, প্রদর্শনীর আয়োজন করা, হারিয়ে যাওয়া কৃতি শিল্পীদের খুঁজে বের করে আলোয় আনা প্রভৃতি। কিছুকাল আগে প্রিন্সেপস- এর উদ্যোগে গুণী চিত্রশিল্পী গোবর্ধন আশের (১৯০৭-১৯৯৬) বড় মাপের একক প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি (Kolkata Centre for Creativity) প্রদর্শকক্ষে। এমনি আরেক সৃষ্টিশীল বিশ্রুতপ্রায় চিত্রকর সুনীল মাধব সেন (১৯১০-১৯৭৯)। প্রিন্সেপস - এর ব্যাবস্থাপনায় তারই বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি নিয়ে প্রদর্শনী হতে চলেছে।
_(1).jpg)
Sunil Madhav Sen (Image Source: Google)
শিল্পকলা নিয়ে লেখালেখির সূত্রেই চিত্রশিল্পী সুনীল মাধব সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ৫২ সি, হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে আমার যাওয়া আসা ছিল। দোতালার একটি ঘরে ছিল তাঁর ষ্টুডিও। সেই ঘরে বসেই শুনেছি তার জীবন ও শিল্পের অনেক কথা ও কাহিনী। তিনি প্রয়াত হন ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর। কিন্তু আমার যাওয়া আসা বন্ধ হয়নি, যতদিন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি অরুণা দেবী জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর (১৫ জানুয়ারী, ১৯৯৭) পর নিঃসন্তান ওই পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়।
সুনীল মাধব সেনের জন্ম ১৯১০ -এর ২৭ অগাস্ট পুরুলিয়াতে। সিভিল সার্ভেন্ট পিতা যতীন্দ্রনাথ ও প্রভাবতী সেনগুপ্তর ছয় ছেলের মধ্যে চতুর্থ সন্তান সুনীল মাধব। মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে মাতৃবিয়োগ হয়। কর্ম উপলক্ষে পিতাকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হতো। তাই শৈশব কেটেছে দাদামশাইয়ের আশ্রয়ে। ছয় বছর বয়েসে চলে যান বাঁকুড়ায়। ভর্তি হন সেখানকার জেলা স্কুলে। ১৯২২ সালে দাদামশাই হরিনাথ রায় প্রয়াত হন। সুনীল মাধব বাঁকুড়া থেকে চলে আসেন কলকাতার জগদীশ রায় লেনের বাসস্থানে। ১৯২৩ সালে ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে। পড়াশুনার পাশাপাশি ভালোলাগা বিষয়বস্তুকে চারকোল ড্রয়িং -এর মাধ্যমে ধরে রাখবার চেষ্টা করতেন। এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অনন্ত পটুয়ার মৃন্ময় মূর্তি গড়া দেখে। প্রসঙ্গ উঠলে সুনীল মাধব বলতেন,
"শৈশবে দেখা সেই ভুবনমোহিনী মূর্তি আজও ভুলতে পারিনি। এতো কাজ দেখেছি, এতো ছবি এঁকেছি, তবুও মনে হয়, সে কাজের যেন তুলনা নেই। বাঁকুড়ার বারো বছরের স্মৃতি ভাঙিয়েই তো হয়েছি আজকের সুনীল মাধব সেন"।
এছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি, সংস্কৃতি শিল্পী মানসে গভীর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।
স্কুল কলেজের গন্ডি পেরিয়ে ১৯৩৭ - ৩৮ সালে সসম্মানে আইন পরীক্ষায় পাশ করে সুনীল মাধব ওকালতি শুরু করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র হিসাবে। কিন্তু একাজে তেমন মন বসছিলো না। নিজেকে দমবন্ধ করা খাঁচার পাখির সঙ্গে মনে হতো। সেই সময়ে ছবি এঁকে উজ্জীবিত হতেন। অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) ও অতুল বসুর (১৮৯৮-১৯৭৭) সান্নিধ্য তাঁর শিল্পচিন্তাকে প্রসারিত করেছিল। শিল্পীজীবনের শুরুতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রতিকৃতি অঙ্কনে। অবয়বগত বস্তুনিষ্ঠতাকে মূর্ত করেছেন বিচিত্র প্রকাশভঙ্গিতে। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিক চেহারা এঁকেছেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য প্রতিকৃতির মধ্যে রয়েছে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাফাইলের চিত্র অনুসারে অংকিত মেরি ও যীশুর ছবিতে অবয়ব সৌন্দর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ১৯৪৮ সালে কলকাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টস -এর বাৎসরিক প্রদর্শনীতে 'ক্লিওপেট্রা' ছবিটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই প্রদর্শনীতে কোনো প্রতিকৃতি নিদর্শন ছিল না। এগুলো কার কার সংগ্রহে, কোথায় আছে তারও কোনো হদিশ পাওয়া যায়না।

Krishna and Radha, Oil Painting
প্রতিকৃতি এঁকে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আঙ্গিক ও মাধ্যমের পরিবর্তন করেছিলেন। তেল রং- কে ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। খুব পাতলা করে কাগজের ওপর তেল রং বুলিয়ে, কাগজ কে টাৰ্পেনটাইন ও জিঙ্ক এ দু একদিন চুবিয়ে রাখতেন। কাগজ শুকিয়ে নিয়ে তারওপর ছবি আঁকতেন। ফলে তেলরঙের ছবি জলরঙের মতো নরম, স্বচ্ছ, ও লাবণ্যময় হয়ে উঠতো। এ প্রসঙ্গে 'টু গার্লস হাস্কিইং ' ছবিটি উল্লেখযোগ্য। এই নির্মাণ প্রক্রিয়া ছিল সুনীল মাধবের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এইভাবেই নিজের পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে।
আঙ্গিক নিয়েও গবেষণা করেছেন। ক্যানভাস-এ রঙের সঙ্গে ছন্দ বজায় রেখে সেঁটেছেন ধাতব পাত। তেলরঙের সঙ্গে গ্লু, মোজাইক দিয়েও চিত্র রচনা করেছেন। এই সময়ের কিছু ছবির মধ্যে 'লার্জ হেড' (গ্লু পেইন্টিং), 'প্রিমিটিভ ফোর্স' (মোজাইক পেইন্টিং), 'প্রিমিটিভ সীল' (ধাতুকে পাত লাগানো পেইন্টিং) উৎকৃষ্ট নমুনা। এই সব চিত্র লক্ষণ পুরাকীর্তির মতো। তৈলচিত্র পুরানো হয়ে কালচে হয়ে গালে যেমন হয় তেমন রং। এ প্রসঙ্গে একাডেমী তে প্রদর্শিত ঢোলবাদিকা, নৃত্যপরা নারী,সিংহাসনে উপবিষ্ট নারী ও দন্ডায়মান নারী ছবি চারটির দিকে তাকানো যেতে পারে। রং ছাড়াও লো-রিলিফ -এ কাজ করায় চিত্ররূপ অনেকটা ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যের মতো হয়ে উঠেছে। অতীত ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে আধুনিকতাকে মিশিয়ে তৈরী হয়েছে এক সুরেলা প্রতিসাকল্প।

Nrityer Tale
সৃজনশীল শিল্পী কখনো একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা রূপকল্পনায় আবদ্ধ থাকেননি। বার বার তা ভেঙেছেন এবং অভিনব শিল্পকৌশল ও প্রকাশভঙ্গি তৈরী করেছেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই চেষ্টা করেছেন বাহ্যিক জীবনের চেয়ে অভ্ভন্তরীন জীবনের মর্ম উদ্ঘাটন করতে। ছোট ছোট রেখার বুননি, অনেকটা মাদুরের মতো দেখতে জমির ওপর জ্যামিতির রেখার টানটোনে অংকিত কয়েকটি চিত্র কিউবিজম -এর সঙ্গে লোকায়তের গভীর সমন্বয়েই মূর্ত হয়েছে। রং ও রেখার বিভাজনে নির্মিত দন্ডায়মান মানুষটির গঠনভঙ্গি একই স্বাদের। কেবল লোকায়ত রীতির মননশীল কয়েকটি ছবি হলো - নৌকায় ভাসমান দুই যাত্রী, সংবাদপত্রের ওপর অংকিত নৃত্যরত নারী এবং বাদ্যযন্ত্রের মুখে মানুষটি। আবার নকশিকাঁথার মতো নকশা করা পটভূমির ওপর আঁকা কয়েকটি রূপবয়বের মধ্যে বাঘ,দুটি মানুষ ও পক্ষির ছবি দৃষ্টিনন্দন। অতি সামান্য রং ও হালকা রেখার একতায় শিব পার্বতী কিংবা আপেল ভক্ষণে উদগ্রীব পক্ষিদ্বয়ের চিত্রভাষে লৌকিক সারল্যের চমৎকার উজ্জীবন ঘটেছে। এই প্রদর্শনীর অন্য আকর্ষণ ছটি মুখাবয়ব। কথায় আছে "Face is the index of mind”, সত্যিই তাই। ছবিগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলে অনুভব করা যায় ক্রোধ, দুঃখ, অভিমান, শান্তি, বিস্ময়, করুনা প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে মুখমণ্ডলে সার্থকভাবে। এর মধ্যে তিনটি মুখ রচিত হয়েছে ভ্যান গঘ -এর মতো টুকরো টুকরো ঢ্যাঁড়া টানার মতো রেখা দিয়ে। অন্য তিনটি উদ্ভাসিত হয়েছে প্রায় ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে। স্ফীতকায়, ভারবহুল নগ্ন দেহাবয়ব চিত্রটি ভাস্কর্যসুলভ, অনেকটা খোদাই করা মূর্তিবৎ। আবার সম্পূর্ণ নিরবয়ব বিমূর্ততার দুটি চিত্র সৃজনকর্মের আর এক বৈশিষ্টপূর্ণ দিক, আদর্শ ও তত্ত্বগত ভাবে।
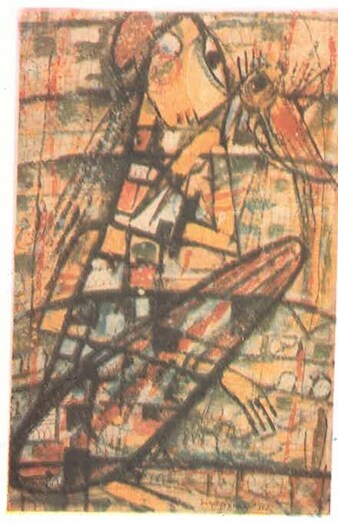
Girl With Bird, Oil Painting
ছবির গঠনপ্রণালীতে রেখার ভূমিকা অপরিসীম। বস্তুর সংস্থাপন, বিন্যাস ও ঘনত্ব সৃষ্টিতে রেখার অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না নিয়েই শিল্পী যে ভাবে বিভিন্ন চরিত্রের রেখার বিন্যাস ও সংযুক্তি ঘটিয়ে স্পন্দন ও ব্যাঞ্জনার সঞ্চার করেছেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখেছেন,
"ছবি দেখলাম। পাঁচ মেশালি। কিন্তু ড্রয়িং এর জোর রয়েছে ছবিতে। আর সবচেয়ে ভালো লাগলো ওর অশিক্ষিত পটুত্ব, যা আমাদের মনে হলো ওঁকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে ওর নিজস্ব অভিব্যাক্তি সাহায্যে। আমরা ওঁকে আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। ১৯৫১ সালে সুনীল বাবু 'ক্যালকাটা গ্রুপ' -এর সভ্য হিসাবে মনোনীত হন।" (স্মৃতিকথা শিল্পকথা: প্রদোষ দাশগুপ্ত। প্রতিক্ষন পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড , ৩ অক্টোবর, ১৯৮৬)
এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণ -এ সুনীল মাধব সেনের চিত্রালংকরণ গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে শিল্পী যে ইলাস্ট্রেশনগুলো করেছেন তা নিঃসন্দেহে চিত্রযোগে ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক।
ভারতীয় শিল্পকলার আধুনিকতার ক্রমবিকাশে ক্যালকাটা গ্রুপ -এর অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই গ্রুপ এর সভ্য দের মধ্যে ছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯১), কমলা দাশগুপ্ত (১৯১৫-২০০১), গোপাল ঘোষ (১৯১৩-১৯৮০), নীরদ মজুমদার (১৯১৬-১৯৮১), পরিতোষ সেন (১৯১৮-২০০৮), প্রাণকৃষ্ণ পাল (১৯১৫-১৯৮৮), সুভো ঠাকুর (১৯১২-১৯৮৫) ও রথীন মৈত্র (১৯১৩-১৯৯৭), গোবর্ধন আশ (১৯০৭-১৯৯৬) এবং আরো কয়েকজন। এই গ্রুপ-এর অস্তিত্ব ছিল ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। সুনীল মাধব এই শিল্পসংগঠনের সভ্য হন ১৯৫১ সালে। দলের সভ্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর শিল্পচিন্তা সুদূর প্রসারী হয়েছিল। যদিও শিল্পী জীবনের প্রারম্ভে রাফায়েল, পিকাসো, রেমব্রাস্ট, গোইয়া, রেনোয়ার, রুবেন্স প্রমুখ দিকপাল পাশ্চাত্য শিল্পীদের ছবি কপি করে শিল্পীকলার অনেক করণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন যা তাঁকে এগিয়ে যেতে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

Musafir
আর্ট কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় সুনীল মাধব বোধ হয় একটা অতৃপ্তি তে ভুগতেন এবং মনে হয় এই অসন্তোষ থেকেই তাঁর অন্তহীন অন্বেষণ। আগেই বলেছি তিনি বারংবার শিল্পশরীরকে ভেঙে আবার নতুন গঠনভঙ্গি তৈরী করেছেন। তাই তাঁর সৃজনে এতো বৈচিত্র বিস্তার। পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী শিল্প, ইউরোপীয় আধুনিকতা, লোকায়ত শিল্পকলা, কিউবিজম, নকশি কাঁথা, তন্ত্রের প্রতীক প্রিমিটিভ আর্ট, গির্জার স্টেইন গ্লাস প্রভৃতি থেকে রসদ নিয়ে একের পর এক ছবি তৈরী করেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতি প্রকরণে। সৃজনে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আলো-অন্ধকারে উদ্ভাসিত, অপ্রমেয় সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত, লৌকিক-অলৌকিকে মেশা কল্পরূপাত্মক এক অভিনব রূপের। ছবিগুলো যেন তাঁর শিল্পচেতনার দর্পন।
শিল্পীর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের অনেকটাই দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালে ওনার জীবন ও শিল্পকলা সম্পর্কে লেখার প্রাক্কালে বাড়িতে সংরক্ষিত ৫০৭ টি শিল্পনিদর্শনের সন্ধান পাই। সেগুলো আজ কোথায় এবং কার সংগ্রহে আছে তা অজানা। প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী হয় ১৯৫০ সালে কলকাতার ১ নং চৌরঙ্গী টেরেসে। তারপর দেশ-বিদেশে কয়েকটি একক ও যৌথ প্রদর্শনী হয়েছে। সুনীল মাধব সেন ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় প্রয়াত হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালে কলকাতার বিড়লা একাডেমী অফ আর্ট এন্ড কালচার-এ শিল্পীর পূর্বাপর ছবি নিয়ে বিরাট চিত্রপ্রদর্শনী হয়। এরপর ১৯৮৮ সালে 'গ্যালারি ৮৮' -এ একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়। প্রস্তাবিত এই প্রদর্শনীটি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে প্রায় ছত্রিশ বছর পর শিল্প রসিক মানুষদের সুযোগ হবে বিশ্রুতপ্রায় সৃষ্টিশীল শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখার।প্রিন্সেপস অতি যত্নসহকারে এই ছবিগুলো দেখার ব্যবস্থা করে আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। আশা করা যায় দর্শকরা বিস্মৃতপ্রায় চিত্রকর সুনীল মাধব সেনের সৃষ্টি বৈচিত্রের রূপরেখা কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন এই প্রদর্শনী দেখে।
প্রশান্ত দাঁ
REFERENCE
সুনীল মাধব সেনের রূপলোক - প্রশান্ত দাঁ